বর্তমানে বাংলা ভাষার সংকট ও উত্তরণ
ড. উৎপল মণ্ডলপ্রফেসর, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়utpalnbu@yahoo.com
ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয়
মর্যাদার দাবিতে সংগঠিত গণআন্দোলন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে
এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরপরই
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয়
নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকেও
অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। সেই প্রেক্ষিতে আমাদের একথা স্বীকার করতেই হবে যে, একুশে
ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দিয়েছে তা মূলত
এসেছে বাংলাদেশের হাত ধরেই। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে আমাদের একথাও স্বীকার
করতেই হবে যে, ভারতীয়
উপমহাদেশের প্রথম ভাষা আন্দোলন হয়েছিল মানভূমে ১৯১২ সালে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের
মধ্যে ভাষা আন্দোলন তীব্র ভাবে ছড়িয়ে পড়ে মানভূমের বাঙালিদের মধ্যে। মানভূমের
এই ভাষা আন্দোলন পৃথিবীতে একটি দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন। ১৯৫৬ সালের আগে পুরুলিয়া
জেলা বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় রাজনৈতিক ভাবে বিহারের স্কুল-কলেজ-সরকারি
দপ্তরে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসের
মাধ্যমে বাংলাভাষী জনগণ হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার চেষ্টা করে; কিন্তু, বাংলা ভাষার
দাবি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পুরুলিয়া কোর্টের আইনজীবী রজনীকান্ত সরকার, শরৎচন্দ্র
সেন এবং গুণেন্দ্রনাথ রায় জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক দল
‘লোকসেবক সঙ্ঘ’ গড়ে তোলেন। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে তাদের সুদৃঢ়
আন্দোলন করেন। ১৯৫৬ সালের এপ্রিলের ২০ তারিখ থেকে মে মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত এক
বৃহৎ পদযাত্রার আয়োজন করা হয়, যা শুরু হয়েছিল পুরুলিয়ার পাকবিররা গ্রাম থেকে, এবং তার
লক্ষ্যস্থল ছিল কলকাতা। এরপর ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার মানভূম জেলা ভেঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্যে সঙ্গে একটি নতুন জেলা যা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলা নামে
পরিচিত তাকে সংযুক্ত করতে বাধ্য হন। এই প্রসঙ্গে আসামের ভাষা আন্দোলনের কথাকে ছেড়ে
দিলে চলে না। আসামের বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা আন্দোলন ছিল আসাম সরকারের অসমীয়া
ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, যেহেতু ঐ
অঞ্চলের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল বাংলাভাষী। এই গণ আন্দোলনের প্রধান
উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ১৯৬১ সালের ১৯মে ঘটে, সেদিন ১১ জন প্রতিবাদীকে শিলচর
রেলওয়ে স্টেশনে আসাম প্রাদেশিক পুলিশ গুলি করে হত্যা করে, যার মধ্যে
একজন নিতান্ত বালিকা - কমলা ভট্টাচার্য। প্রথম নারী ভাষা শহীদ এবং তা বাংলা ভাষার
জন্য।
বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের সাথে বাকি দুটি
আন্দোলনের কথা এ ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক কারণ, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার সম্মান
রক্ষার জন্য তিন তিনবার আন্দোলন হয়েছে এবং খুবই গর্বের বিষয় প্রত্যেকবার সে
আন্দোলনে জয়ীও হয়েছে। এটাই আমাদের বাংলা ভাষার সুবিশাল ইতিহাস। কিন্তু খুবই
দুঃখের সাথে লক্ষ করা যায় এই ঐতিহ্যময় বাংলা ভাষার চারপাশে ঘনিয়ে এসেছে সংকটের
ঘন ছায়া। এবার প্রশ্ন হল,
এই সংকটটি কতটা গভীর?
আদৌ কি আমরা বাংলা ভাষাকে সংকটের পর্যায়ে ফেলতে পারি? একটু ভেবে
দেখলে উপলব্ধি করা যাবে,
আজ থেকে ১৫-২০ বছর আগে যদি আমরা ফিরে যাই, তখন কিন্তু আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা
দিবস এতখানি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পালিত হতো না। কিন্তু বর্তমানে আমরা বাঙালিরা
রীতিমতো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই দিনটিকে পালন করে চলেছি। দেখুন, একটি বিষয়
তখনই ‘উদ্দেশ্য’ হয়ে ওঠে যখন তার নিখুঁত ‘প্রয়োজন’ জন্মায়। আমরা হেলথ চেকআপ
তখনই করাতে যাই, যখন
আমাদের শরীর কিছু ভুলের সংকেত দেয়। একই কথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের
ক্ষেত্রে ও সমানভাবে প্রযোজ্য। আমরা পালন করছি, কারণ পালন করবার প্রয়োজন পড়েছে, মানে অসুখ
করেছে। হয়তো অসুখটি এখনো গুরুতর নয়, তবে অসুখ হয়েছে। আর সেটা যে হয়েছে
ইউনেস্কো বর্ণিত তথ্য তা প্রমাণিত করে দেয়, তবে শুধুই যে সেটা বাংলা ভাষার জন্য
প্রযোজ্য এমনটা নয়। পৃথিবীর এমন অনেক
ভাষাই রয়েছে যা নিত্যদিন বিলুপ্তির পথে
এগিয়ে যাচ্ছে। যাকে আমরা বলি “Endangered language”। হ্যাঁ, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ছাড়াও
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় ২৫ কোটি মানুষের মাতৃভাষা
বাংলা। তা সত্ত্বেও ইউনেস্কোর একটি রিপোর্ট বলছে যে, প্রতি ১২ দিনে পৃথিবীতে একটি করে
ভাষার মৃত্যু ঘটে, তার
মানে এটা তো স্বীকার করতেই হবে যে প্রতিদিন কোনো-না-কোনো জননী মৃত্যুবরণ করে
চলেছেন এবং সেই হিসেব অনুযায়ী জার্মানির একটি গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে আগামী ১০০
বছরের মধ্যে এই ২৫ কোটি সন্তানের জননী একেবারে মৃত্যুবরণ না করলেও তাকে যেতে হবে
বৃদ্ধাশ্রমের নিঃসঙ্গতায়। এবার প্রশ্ন হল বিষয়টি কি আদৌ সেই রকম? এখানেই আমার
মূল আলোচনার জায়গাটি। পৃথিবীর যে কোন সহৃদয়বান, অনুভূতিশীল, চিন্তাশীল
ব্যক্তি প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে
এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন। তা যদি না হতো তাহলে ভবানীপ্রসাদ মজুমদারকে কেন লিখতে
হয়, 'জানেন
দাদা আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না' !
এবার এই সংকটের চিত্রটিকে
সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে, আমার মতে চারটি পর্যায়ক্রমে অবশ্যই ভাবা দরকার-
(১) বাংলা
ভাষার অধিকার।
(২) বাংলা
ভাষার ক্ষমতা।
(৩) বাংলা
ভাষার বর্তমান পরিস্থিতি।
(৪) বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায়।
অধিকারের কথা বলতে হলে প্রথমেই বলতে হয়, হাজার বছর
ধরে সমৃদ্ধপূর্ণ ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে। যদিওবা স্বাধীনতার পরে তার ধরনটা একটু বদলে
যায়। আমাদের যে এই দুই বাংলা ভাষার দেশ একদিকে ভারতের ক্ষুদ্রতম অংশ পশ্চিমবঙ্গে
এবং অন্যদিকে বাংলাদেশে,
যদিও বাংলাদেশ নিজেকে বাংলা ভাষায় সাবলীল করে তুলতে পেরেছে, কিন্তু
ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি এবং তার কারণও রয়েছে বটে, ভারতবর্ষ
একটি বিভিন্ন ভাষাভাষীর দেশ, সেখানে কেবলমাত্র একটি ভাষা কে নিয়ে চলা রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে
সম্ভব নয়। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হল, রাষ্ট্রীয়
দৃষ্টিভঙ্গিটা যদি আমরা ছেড়েও দিই তবুও আমাদের যেটুকু অধিকার বা ক্ষমতা রয়েছে
বাংলা ভাষাকে অক্ষত রাখবার,
সে সম্পর্কে কি আমরা খুব সচেতন? প্রশ্নটা এখানেই। আমাদের ব্যক্তিগত
জীবনের দৈনন্দিন কাজ গুলো যেমন নানা ধরনের ফর্ম ফিলাপ, নানা ধরনের
আবেদন পত্র লিখন, সোশ্যাল
মিডিয়ায় নিজের পরিচয় জ্ঞাপন এই কাজগুলো আমরা ইচ্ছে করলেই মাতৃভাষায় করতে সক্ষম,
সরকার তার সুবিধাও দেয় বটে। কিন্তু তবুও বাঙালি সেখানে মাতৃভাষার বদলে ইংরেজিকেই
বেছে নেয়। তাই বলে কি ইংরেজিতে লেখা উচিত নয়? অন্য কোন পথ না থাকলে অবশ্যই
ইংরেজিতে লেখা উচিত এবং তারসাথে নিজের বাংলা ভাষার যতটুকু অধিকার খাটানো যেতে পারে
সেই জায়গাটুকু অবশ্যই ব্যবহার করা দরকার। আর এই প্রসঙ্গে উঠে আসে আত্মসমালোচনা।
নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে। আমরা বাংলাভাষার সংকট বলছি কিন্তু সেই সংকট আমাদের
অধিকারগুলোকে না বোঝার ফলে কতটা উঠে আসছে, সেই জায়গাগুলো আমাদের ধরতে হবে।
এরপর আসি আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের
আলোচনায়- বাংলা ভাষার ক্ষমতা। দেখুন, বাংলা ভাষার এই ক্ষমতাটুকু তো আছে যে, মাতৃভাষার
আঁচল ধরে আমাদের যাবতীয় বক্তব্য বাংলায় বলতে পারি, লিখতে পারি, প্রকাশও
করতে পারি। সেই ক্ষমতা যদি নাই থাকতো তাহলে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের বুকে
সত্যেন্দ্রনাথ বসু ‘বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ’ তৈরি করেছিলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান
চর্চার জন্য। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, মহেন্দ্রলাল
বসু, অমৃতলাল
বসু বাংলায় লিখেছেন। অমৃতলাল বসু বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ১৯১৪ সালে। সেই
সময় ‘পথ’ বলে একটি পত্রিকা বার হতো যার সম্পাদকমন্ডলী তে ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র
মহলানবিশ। সত্যচরণ লাহার আরেকটি পত্রিকায় সেসময় চলচ্চিত্র এবং বেতার এর টেকনোলজি
বিষয়ে একের পর এক লেখা বেরিয়েছে। প্রকৃতি নিয়ে এখনকার সময়ে আমরা নানা রকম
চর্চায় আবদ্ধ হয়েছি সেই সময় ‘প্রকৃতি’ নামেই জগৎ লাহা বাংলায় লেখা পত্রিকা বের
করতেন। অথচ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়ার পর লক্ষ্য করা যায় এর উল্টো চিত্র। এবং
এই একুশ শতকে এসে মানুষের ব্যস্ততা এবং চিন্তা করার শক্তি যত কমছে তত এই বিপরীত
প্রবণতা বাড়ছে। তবে তা অবশ্যই হীনমন্যতার সাক্ষ্য বাহী। একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা
বলি, আমি বহু বন্ধুবান্ধবকে জানি যারা সত্যিই অন্য ভাষায় পারদর্শী, এমনকি এই সময়েও যারা অধিকাংশ সময় বাংলা বা ভারতের বাইরেই থাকে, তারা কিন্তু
বাংলায় এসে অকারনে একটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে না! অধিকাংশ হীনমন্য বাঙালি আজ
ভুলে যায় যে মধুসূদন দত্ত,
উৎপল দত্ত, সত্যজিৎ
রায় বাংলাতেই লিখেছেন। আসলে চিন্তার দৈন্যতাই এই হীনমন্যতার অন্যতম কারণ।
বর্তমানে কলোনিয়াল হ্যাংওভার গ্রস্থ বহু বাঙালির এই অবস্থা। হীনমন্যতায় ভোগা
কিছু বাঙালির এই মানসিকতার পরিচয় একটু আধটু পাওয়া যায় আগেও। তা না হলে একশ বছর
পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ খোলার সময় তৎকালীন উপাচার্য মহাশয় কে
অত কথা শুনতে হতো না! এবং আরো মজার ব্যাপার, বাংলার ছাত্র দের যে প্রথম ব্যাচটি
বেরিয়েছিল, তাদের
আবার বাংলা পরীক্ষা দিতে হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়! অর্থাৎ বাঙালির এ রোগ বহু পুরনো, এবং
পরিবেশগত কারণে সে রোগ এখন মহামারি’র দিকে এগোচ্ছে।
এবার আসি আমার আলোচনার তৃতীয় পর্যায়ে-
বাংলা ভাষার বর্তমান পরিস্থিতি। বাঙালির
এইযে রোগ যা মহামারীর আকার ধারণ করেছে তার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। একটু
বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বোঝা যাবে, বাংলা ভাষাটা ধারণক্ষমতা অনেকটাই
বেশি। ইংরেজি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি
প্রভৃতি ভাষা থেকে অনেক শব্দ ঢুকে বাংলা ভাষাকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। এই ‘Assimilation’ প্রক্রিয়া
ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ সেটা জোরপূর্বক হচ্ছে না। এখানে জোরপূর্বক বলতে ‘মানসিক
আগ্রাসন’ প্রক্রিয়াটাকে আমি বোঝাতে চাইছি। এটির একটি ভালো উদাহরণ হল, ব্রিটিশরা
যখন আমাদের দেশে মূলত ব্যবসা বাণিজ্য সূত্রপাত করে এবং আস্তে আস্তে তারা আমাদের
দেশকে অধিকার করা শুরু করে এবং তারপরে চলে মানসিক আগ্রাসন। যাকে আমরা ‘Colonialism’ বলতে
অভ্যস্ত। এক্ষেত্রে তারা ‘white supremacy’-কে প্রচার করা শুরু করে। অর্থাৎ
ইংরেজরা যে ভাষায় কথা বলে যা তাদের আচার-আচরণ যাবতীয় কিছু যা কিছু তারা দৈনন্দিন
জীবনে ব্যাবহার করে থাকে তা সবকিছু ভালো, আর সেটা ব্যতীত যাবতীয় কিছু খারাপ। এই
ধারণা তারা মুলত নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল বশ্যতা স্বীকার করাবার জন্য, আর আমি যে
সময়ের কথা বলছি সেটা শিল্পবিপ্লব উত্তর যুগের কথা, তখন তারা এসেছিল বাণিজ্য করতে।
কিন্তু এখন সেটা বাণিজ্য পর্ব নয় এখন তার চুড়ান্ত বিকাশ পর্ব ‘Consumerism’ বা
‘পণ্য সভ্যতা’ চলছে এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে ‘বিশ্বায়ন’। ফলে যে ভাষা যত বেশি
অন্য ভাষার বাহকদের হীনম্মন্যতাবোধে ভোগাতে পারবে, ততটাই বেশি পরিমাণে নিজের মানসিক
আগ্রাসনের রাজত্বকে, সংস্কৃতির
রাজত্বকে বিস্তার যেমন করতে পারবে, তেমনি নিজেদের দেশীয় পণ্য কে বিক্রিয়ও
করতে পারবে বেশি। যে কারণেই নানা ফোরস্টার, ফাইভস্টার রেস্টুরেন্টে খুব
নিম্নমানের খাবারও উচ্চমানের ইংরেজি বাচনভঙ্গিতে বিক্রি করা হয়। তাই বলে কি নিজের
ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানা উচিত নয়? অবশ্যই উচিত। যত বেশি ভাষা জানা থাকে, ততটাই বেশি
জ্ঞানের পরিধিও বাড়তে বাধ্য। কিন্তু সেক্ষেত্রে শর্ত একটাই, নিজের মাতৃভাষাকে
অবহেলা করে অন্য ভাষার ‘supremacy’-কে স্বীকার করে নেওয়া, এই মানসিক
প্রবৃত্তির বিকাশে কখনোই সহমত থাকা উচিত নয়। এখানে জীবনানন্দ দাশের কবিতার একটি
লাইন খুব মনে পড়ে যাচ্ছে,
যার দ্বারা বাঙালির মানসিক পরিস্থিতির কথা খুব সহজে বোঝানো যায়-
“অপরের মুখ
ম্লান ক’রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।”
‘এই সব
দিনরাত্রি’
জীবনানন্দ দাশ
আর এখানেই চন্দ্রিল
ভট্টাচার্য কে উন্মোচিত করে দিতে হয় হীনমন্য বাঙালির এক অদ্ভুত আত্ম সুখের
মনস্তত্ত্ব - দুজন বাঙালি, আর অন্যান্য বাঙালির সামনে ইংরেজীতে কথা বলতে পারলে যে সুখ
পায় তা আর কোথাও পায় না! এই প্রেক্ষিতেই ভাবতে হবে বাংলা ভাষার বর্তমান সংকট কে।
এবার আসি মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসনের বাস্তব
প্রেক্ষিতে। দেখুন, একটি
প্রশ্ন আমার মনের সর্বদা বিচরণ করে, আচ্ছা এই যে আগ্রাসনী মনোবৃত্তি
পৃথিবীতে কার নেই? যে
কোন দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ, গোষ্ঠী এবং একদম ক্ষুদ্রতম এককে যদি আমরা চলে যাই
তাহলে দেখা যাবে প্রতিটি মানুষ ক্রমশ আগ্রাসন মনোবৃত্তি প্রতিফলিত করছে। এমনকি
যেসব পাঠকেরা আপনারা যারা আমার লেখাটি পড়ছেন, তাদের প্রতি আমার বক্তব্যকে আমি যে
চাপিয়ে দিচ্ছি না সে কথা কেউ বলতে পারবে? এই মনোবৃত্তি মানুষের একটি সহজাত
প্রবৃত্তি এটি আজীবন ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কারোরই এখানে
কোন দোষ নেই, সবটাই
নিহিত আছে আত্ম চেষ্টার উপরে। কে কতটা নিজেকে বশ হতে দিচ্ছে, আর কে তার
অধিকার কে টিকিয়ে রাখতে পারছে এর মধ্যেই সমস্ত খেলাটি ঘূর্ণায়মান।
প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে
রাখা দরকার, আমরা
প্রায়ই এই মানসিক আগ্রাসন মনোবৃত্তিটাকে
বিশ্বায়নের মারফত ন্যায়সংযত করে তুলতে চাই। কিন্তু এখানে বলে রাখা দরকার ‘Globalization’ বা ‘বিশ্বায়ন’
এখন অতীত। এখন গ্লোবালাইজেশন পার করে আমরা পৌঁছে গেছি গ্লোলোকালাইজেশনে। যদি
আমরা আমাদের আত্মশক্তিকে অক্ষত রাখতে পারি তাহলে পৃথিবীর কাছে আমাদের পৌঁছে যেতে
হবেনা, পৃথিবীই
আমাদের কাছে আসবে। এবার আমরা একদম আলোচনা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, আমরা এতক্ষন
নানা সংকট, সংকটের
প্রভাব, সংকটের
ধরন এবং মানসিক আগ্রাসন রীতির নানা দিক আলোচনা করলাম। তাহলে প্রশ্ন হল এই সঙ্কট
থেকে কোনদিন কি আমরা বেরোতে পারবো না? যদি পারি তাহলে তার রূপটা কি রকম হবে? আমার মতে
একমাত্র ত্রিশক্তি ভাবনার দ্বারাই আমরা এই সংকটের মোকাবিলা করতে পারি। ত্রিশক্তি বলতে মূলত তিনটি শক্তির মিলিত রূপকে
বোঝাতে চেয়েছি। সেই শক্তি গুলি হল-
(ক)
আত্মশক্তি
(খ) যৌথ
শক্তি
(গ)
চিন্তাশক্তি
প্রথম কথা হল বর্তমান যুগের
প্রেক্ষিতে আমাদের মধ্যে আত্ম শক্তির জাগরণ
ভীষণভাবে দরকার। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে আবার ফিরে যেতে হয়-
“যার ভয়ে
তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি
জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;
যখনি
দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথকুক্কুরের
মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে ;
দেবতা
বিমুখ তারে, কেহ
নাহি সহায় তাহার,
মুখে
করে আস্ফালন, জানে
সে হীনতা আপনার
মনে
মনে।”
“এবার ফিরাও মোরে”
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এখানে আমাদের মনে সেই
আত্মশক্তি টাকে জাগ্রত করতে হবে। আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে অন্যের ভিন্ন
ভাষার বাচনিক ক্ষমতা দেখে, আমরা কেন নিজেদেরকে হীনমন্যতায় ডোবাবো? আমরা যদি
একটু সচেতন ভাবে দেখি জাপান, চীন,
রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলো তারা তাদের নিজস্ব মাতৃভাষার জোরে পুরো পৃথিবীর সামনে
নিজেদেরকে প্রমাণিত করতে পেরেছে, তারা কখনোই আত্মগ্লানিকে উন্নতির মাঝে আসতে দেয়নি। একেই
আমি বলছি আত্মশক্তির জাগরণ।
এবার আসি যৌথ শক্তির
প্রসঙ্গে। এখানেই হয়তো বাঙালি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বাঙালি এখন যৌথ হতে পারছে না।
আমরা তথাকথিতভাবে ‘উন্নত’ শব্দটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি। আমরা সদা ব্যস্ত
এটা দেখানোর জন্যই যে, কে কার থেকে বেশি উন্নত। কিন্তু একটু গভীর ভাবে দেখলে লক্ষ
করা যায় বাঙালি এযাবত যত উন্নতির পথে হেঁটেছে ততোবারই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমরা
সর্বদাই দেখতে পারি,
কোন ব্যক্তি বাংলায় বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং অপর আরেকজন ব্যক্তি যদি তিনি
ইংরেজিতে বক্তৃতা দেন,
সেখানে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়া ব্যক্তিটি বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া ব্যক্তিটিকে
নিছক অবহেলা ছাড়া আর কোন চোখে দেখতে পারেন না। এই অবহেলার প্রশ্ন কখনোই আসা উচিত
নয়। এখানে আমরা যদি একত্রিত হয়ে আমাদের নিজের মাতৃভাষাকেই বক্তব্যের মাধ্যম
হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাই,
তবেই যৌথ শক্তি সার্থক। দেখুন, সংকট যেহেতু একদিনেই আসেনি, ফলে তার
সমাধান একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং যৌথ
শক্তিকে প্রাধান্যতা দিতে হবে।
এবার এই প্রসঙ্গেই চলে আসে চিন্তাশক্তির
কথা। এই শক্তিটি একদম আমার বিশ্বাসের জায়গা। বর্তমান যুগে আমরা সারা পৃথিবীর
প্রেক্ষিতে যদি লক্ষ করি,
তাহলে দেখা যাবে কিভাবে মানুষের চিন্তাশক্তিকে বিনষ্ট করে দেওয়া যায় তা
নিয়েই চলছে মহাযজ্ঞ। মানুষের চিন্তা করতে
শিখলেই সে প্রশ্ন করা শুরু করে, আর সেই প্রশ্নই মানুষকে নেশাগ্রস্ততা
থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করে। আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষাকে ভালোবেসে আমাদের
চিন্তাশক্তিকে সমৃদ্ধ করতে পারি তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি পারবেনা আমাদের পিছিয়ে
রাখতে। গ্লোলোকালাইজেশন এটার একটি ভাল দিক। এর উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ
বিবেকানন্দ কে ছেড়ে দিলেও সাম্প্রতিক অতীতের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাব
সত্যজিৎ রায় বা উৎপল দত্ত কে। সত্যজিৎ অস্কার জয়ী হয়েছেন বাংলাতেই সিনেমা করে।
চিত্রকর যামিনী রায় বা ভাস্কর রামকিঙ্কর ইংরেজি কেন বাংলা ছাড়া আর কোন ভাষায়
জানতেন না। কিন্তু তাদের চিন্তার উৎকর্ষের জন্যই তাদের শিল্প পৌঁছে গেছে বিশ্বের
দরবারে। যামিনী রায়কে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার জন্যই বিষ্ণু দের মতন পন্ডিত
তার শিল্পকর্ম নিয়ে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখেন। অর্থাৎ কোয়ালিটিই আসল কথা। আর এই
কোয়ালিটি ঠিক রাখতে মাতৃভাষার মাধ্যমে চিন্তাই একমাত্র সহায়ক। তার কারণ আগেই
বলেছি। সত্যজিতের ছবিতে গুপী-বাঘা কে বলতে শুনি-- সাদাসিধা মানুষ মোরা দেশে দেশে যাই/
নিজের ভাষা ভিন্ন মোদের ভাষা জানা নাই। লক্ষ্য করার বিষয়, তারা বলছে, নিজের ভাষা
ছাড়া অন্য ভাষা জানে না কিন্তু সেই ভাষা নিয়েই পৌঁছে গেছে রাজদরবারে! এটাই
কোয়ালিটি।
এই কোয়ালিটিটাকে আমাদের অক্ষত রাখতে হবে।
আর এটা যদি আমরা অক্ষত রাখতে পারি তাহলে একশ কেন এক হাজার বছরেও আমাদের মাতৃভাষার
সার্বিক দিক ঠিক থাকবে। হ্যাঁ, অবশ্যই কিছুটা বিবর্তিত হবে আর সেটা স্বীকার্য। কারণ
বিবর্তন ছাড়া মানব জীবনের ইতিহাস কখনোই গড়ে উঠতে পারে না। সেই গুহা থেকে
কম্পিউটার পর্যন্ত এটাতো বিবর্তনই, তাকে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু চিন্তাশক্তিতে ক্ষমতা থাকলে আমরা কখনোই
অবলুপ্তির পথে যাব না,
এটা আমার বিশ্বাসের জায়গা। এই ত্রিশক্তি আত্মশক্তি, যৌথ শক্তি
এবং চিন্তাশক্তি কে মিলিয়ে আমাদের কয়েকশো বছর পুরনো বৃদ্ধা ভাষা জননীকে রক্ষা
করতে পারবো, নতুবা
একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে, নিজের দায়িত্বকে এড়িয়ে দিয়ে নিজের
মাতৃভাষাকে সংকটের মুখে ঠেলে দেবো আমরা নিজেরাই। আত্মবিস্মৃত বাঙালির এই
ত্রিশক্তিবোধ জাগ্রত না হলে বছরের পর বছর তৈরি হবে শুধু হাঁসজারু। আর যে মায়ের
পঁচিশ কোটি সন্তান ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়, তাকেও একদিন বৃদ্ধাশ্রমের
নিঃসঙ্গতায় গিয়ে, ধীরে
ধীরে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এখনো সময় আছে ঘুরে দাঁড়ানোর।
……………………………..


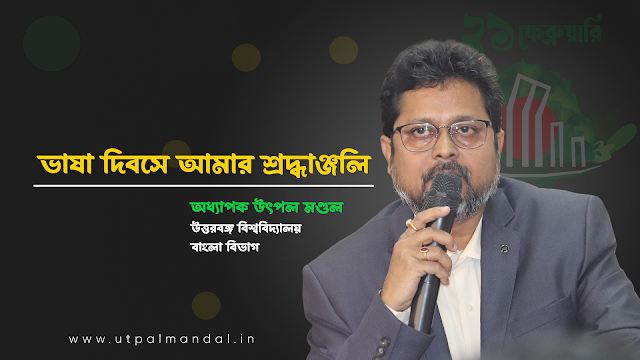



No comments:
Post a Comment